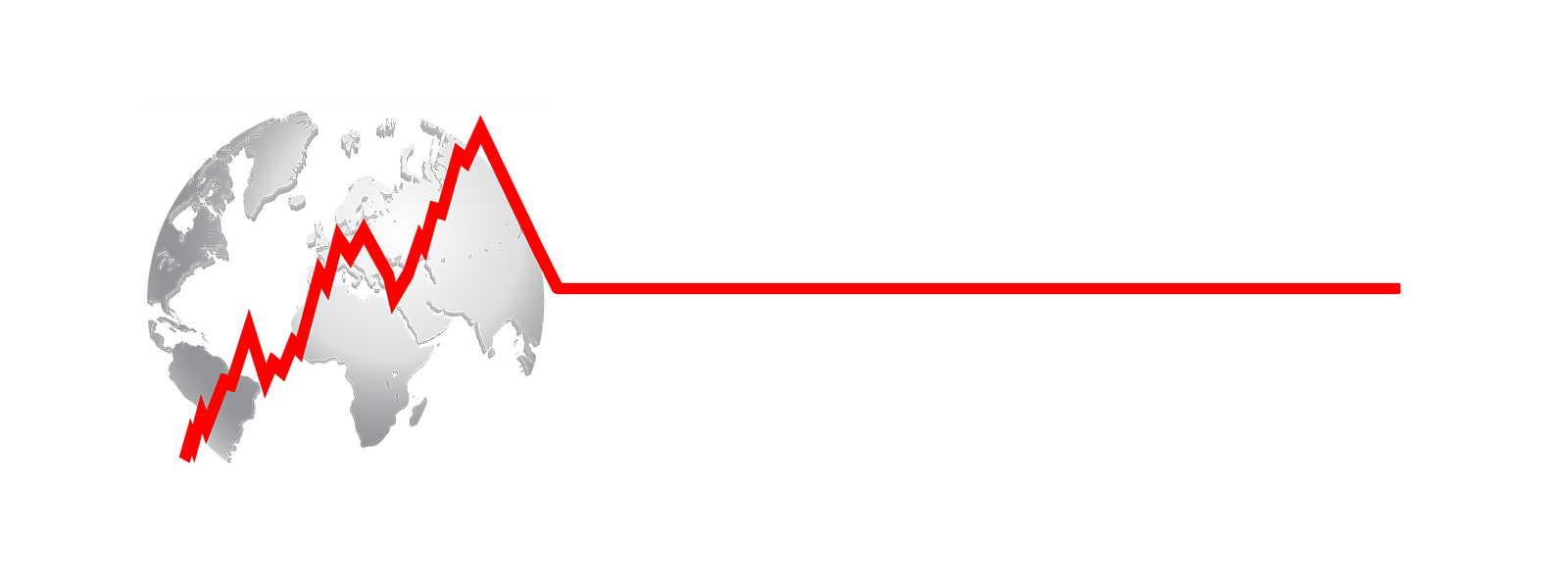বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের ইতিহাস (১৯৭১ সালের পর)
ভূমিকা
বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হলো টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক শিল্প। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই খাত অভাবনীয় অগ্রগতি করেছে। ১৯৭১ সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দেশের শিল্পখাত কীভাবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হলো — তা একটি অনুপ্রেরণামূলক ইতিহাস। এই প্রবন্ধে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশ, চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের কথা বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের অবস্থা
স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল বিধ্বস্ত। অধিকাংশ শিল্প-কারখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল এবং অভিজ্ঞ জনবল ও প্রযুক্তির অভাব প্রকট ছিল। এ সময় প্রায় ৮২টি টেক্সটাইল মিল রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয় এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (BTMC) গঠিত হয়। এইসব রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা মূলত অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য কাজ করত; রপ্তানির ধারণা তখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি।
সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা এই মিলগুলোর বড় সমস্যা ছিল:
উৎপাদনশীলতার অভাব
প্রযুক্তির পশ্চাদপদতা
দক্ষ কর্মী সংকট
প্রশাসনিক দুর্নীতি ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা
ফলে শিল্পের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।
১৯৭২–১৯৮০: জাতীয়করণ ও শিল্পের পুনর্গঠন
স্বাধীনতার পর সরকার সমাজতান্ত্রিক নীতিতে শিল্পখাত জাতীয়করণ করে। BTMC এর মাধ্যমে মিলগুলো পরিচালিত হলেও বাস্তবে উৎপাদন হ্রাস পায়। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রেও কারখানাগুলো অক্ষম হয়ে পড়ে।
এই সময়ের বড় ঘটনা ছিল বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের (Ready-Made Garments – RMG) চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া। ১৯৭৪ সালে চালু হওয়া মাল্টি-ফাইবার এগ্রিমেন্ট (MFA) উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরি করে।
এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কিছু ব্যক্তি উদ্যোগ শুরু হয়, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি গড়ে দেয়।
১৯৮০-এর দশক: গার্মেন্টস শিল্পের উত্থান
১৯৭৮ সালে দেশ গার্মেন্টস নামের একটি প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কোরিয়ার ডাইউ কর্পোরেশন এর সাথে চুক্তি করে এবং ১৩০ জন বাংলাদেশি কর্মীকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণের জন্য পাঠায়। তারা ফিরে এসে দেশে আধুনিক পোশাক কারখানা প্রতিষ্ঠা করে।
এরপর দ্রুত শত শত গার্মেন্টস কারখানা গড়ে ওঠে। বিশেষ করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম এলাকায় এ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাগুলো ছিল:
কম মজুরি
পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি
যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার (GSP সুবিধা)
উদ্যোক্তাদের উদ্যোগী মনোভাব
এ সময়ের মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প অভ্যন্তরীণ বস্ত্র খাতকে ছাপিয়ে যায়।
মূল উন্নয়নসমূহ: ১৯৮০-৯০ এর দশক
১. রপ্তানি বৃদ্ধি
১৯৮৩ সালে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩১ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৯৮ সালের মধ্যে বেড়ে ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়।
২. নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ
মিলিয়নেরও বেশি নারী গ্রামীণ এলাকা থেকে এসে গার্মেন্টস শিল্পে কাজ শুরু করেন। এটি নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৩. ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের বিকাশ
গার্মেন্টস শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা, কাপড়, বোতাম, জিপার ইত্যাদি উৎপাদনকারী শিল্প গড়ে ওঠে, যা আমদানির উপর নির্ভরতা কমায়।
৪. প্রাইভেট খাতে প্রবৃদ্ধি
সরকার ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় টেক্সটাইল মিলগুলো বেসরকারিকরণ শুরু করে এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ উৎসাহিত করে।
৫. প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
BGMEA (বাংলাদেশ গার্মেন্টস প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি) এবং BKMEA (বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি) গঠন করা হয় উদ্যোক্তাদের সংগঠিত ও সহায়তার জন্য।
২০০০ সালের পর: নতুন চ্যালেঞ্জ ও অভিযোজন
বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়:
MFA সমাপ্তি (২০০৫): কোটা সুবিধা শেষ হয়ে গেলে চীন, ভারত ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতা শুরু হয়।
কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার ইস্যু:
রানা প্লাজা দুর্ঘটনা (২০১৩) আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের পোশাক খাতের খারাপ চিত্র তুলে ধরে।
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন:
আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।
তবে উদ্যোক্তাদের দ্রুত অভিযোজন ক্ষমতা এবং শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশ শিল্প খাতে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকে এবং দ্রুত উন্নতি ঘটায়।
বর্তমান অবস্থা: বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব
বর্তমানে বাংলাদেশ:
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক (চীনের পরে)
প্রতিবছর ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করছে (২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী)
প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিককে সরাসরি কর্মসংস্থান দিচ্ছে
তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বের বড় ব্র্যান্ডগুলোর (যেমন: H&M, Walmart, Zara, Uniqlo) নির্ভরশীলতা তৈরি করেছে
এখন বাংলাদেশে রয়েছে:
স্পিনিং মিল (সুতা উৎপাদন)
উইভিং ও নিটিং ইউনিট (কাপড় তৈরি)
ডাইং ও ফিনিশিং ফ্যাক্টরি (রঙ ও কাপড়ের উন্নয়ন)
গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি (চূড়ান্ত পোশাক তৈরি)
ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পও (বোতাম, লেবেল, জিপার) দারুণভাবে প্রসারিত হয়েছে।
সাম্প্রতিক প্রবণতা
১. সবুজ (Green) ফ্যাক্টরি
বাংলাদেশের অনেক পোশাক কারখানা এখন পরিবেশবান্ধবভাবে নির্মিত, যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।
২. পণ্যের বৈচিত্র্য
শুধু টি-শার্ট বা প্যান্ট নয়, এখন বাংলাদেশ উচ্চমূল্যের পোশাক যেমন: ব্লেজার, আন্ডারগার্মেন্টস, স্পোর্টসওয়্যার ইত্যাদি তৈরি করছে।
৩. উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি গ্রহণ
ডিজাইন, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ও ইকো-ফ্রেন্ডলি কাপড়ের দিকে মনোযোগ বাড়ানো হচ্ছে।
৪. শ্রমিক উন্নয়ন
নতুন আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মজুরি উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে, যদিও আরো উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে।
ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ
অটোমেশন
রোবটিক্স ও মেশিনের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে শ্রমনির্ভর উৎপাদন ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
নতুন প্রতিযোগী
ভিয়েতনাম, ইথিওপিয়া, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ পোশাক রপ্তানিতে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে।
পরিবেশগত সমস্যা
টেক্সটাইল শিল্প অনেক পানি ও শক্তি ব্যবহার করে এবং পরিবেশ দূষণ করে। তাই টেকসই উৎপাদনের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে।
শ্রমিক অধিকার
কাজের পরিবেশ, ন্যায্য মজুরি এবং শ্রমিকদের মর্যাদা নিশ্চিত করাই বড় চ্যালেঞ্জ।